বৃহস্পতিবার, ০১ মে ২০২৫, ১১:৩০ পূর্বাহ্ন
সংবাদ শিরোনাম ::
সাতক্ষীরার সেই ঐতিহ্যবাহী গুড়পুকুর মেলা
- আপডেট টাইম : বুধবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১, ৬.২৭ পিএম
- ২০৭ বার পঠিত

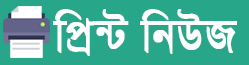
মিহিরুজ্জামান জেলা প্রতিনিধি সাতক্ষীরাঃ
সাতক্ষীরা জেলার লৌকিক আচার আচরণ বিশ্বাস আর পৌরাণিকতায় সমৃদ্ধ নানা কিংবদন্তির প্রবহমান ধারায় সজীব এখানকার ঐতিহ্য। বঙ্গোপসাগরের আঁচল ছোঁয়া সুন্দরবন, আর সুন্দরবনকে বুকে নিয়ে সমৃদ্ধ এখানকার প্রকৃতি, এমনকি অর্থনীতিও।সুন্দরবনের চোখ জুড়ানো চিত্রল হরিণ, বিশ্ববিখ্যাত রয়েলবেঙ্গল টাইগার (ডোরাকাটা বাঘ) থেকে শুরু করে নদ-নদী, বনদেবী, বারো ভূঁইয়ার অন্যতম রাজা প্রতাপাদিত্যের রাজধানী, বিভিন্ন মোঘলীয় কীর্তি, অসংখ্য প্রতিনিদর্শন,পুরাকালের কাহিনী, জারী-সারী, ভাটিয়ালি, পালাগান, পালকী গান এসবের মধ্যেই সাতক্ষীরার মানুষের আত্মীক পরিচয় গ্রন্থিত।এখানে জন্মেছেন দেশ বরেণ্য কবি, সাহিত্যিক, কণ্ঠশিল্পী, চিত্রকর, জন্মেছেন জীবন সংগ্রামে ঋদ্ধ সংগ্রামী মানুষ। শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর আত্মত্যগী বীর। তিঁতুমীরের বাঁশের কেল্লার হয়ে যেমন লড়েছেন, তেমনি মহান ভাষা আন্দোলনে এবং মহান মুক্তিযুদ্ধেও বীরত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন গ্রাম বাংলার লোকজ ঐতিহ্যই এখনও পর্যন্ত সাতক্ষীরার সংস্কৃতির মূলধারাটি বহন করে চলেছে। খুব সহজেই এখানে মিলিত হয়েছে লৌকিক আচার-আচরণের সাথে পৌরাণিতত্বের। যেন দুটো নদীর সম্মিলিত এক বেগবান ধারা। বছরের প্রায় প্রতিটি সময় ধরে অগুনতি মেলা বসে সাতক্ষীরায়। সাগরদ্বীপ দুবলা থেকে শুরু করে খুলনা, যশোর, ঢাকা, বিক্রমপুর, ফরিদপুর এমনকি একসময় পশ্চিমবঙ্গেও এর প্রভাব ছিল। এ জেলার শুধু নয় দক্ষিণ বাংলার সবচেয়ে বড় লোকজ মেলাটি বসে সাতক্ষীরা শহরেই, পলাশপোলে, গুড়পুকুরের পাড়ে।গুড়পুকুরের নামানুসারেই মেলার নামকরণ করা হয়েছে ‘গুড়পুকুরের মেলা’। মেলাটির বয়স এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি। মেলা নিয়ে অতীতেও তেমন লেখালেখি হয়নি। মেলাটির উৎপত্তি খুঁজতে কয়েকজনকে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম নব্বইয়ের দশকে।মরহুম সোবহান খান চৌধুরির (৮০) বক্তব্য এ রকম: অনেক পথ হেঁটেছেন আজ। ক্লান্তিতে পা আর উঠতে চায় না। শেষ ভাদ্রের ভ্যাপসা গরমে মিইয়ে এসেছে সমস্ত শরীর। ওই যে, গৌরদের পুকুর পাড়ের বটগাছটা। ওর ছায়ায় একটু জিরিয়ে নেয়া যাক। বটের ছায়ায় বসতে না বসতেই ঘুম এসে গেল ফাজেল চৌধুরীর, শেকড়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন তিনি। গাছতলার ঘুম, গাছের ছায়ার মতই ছেঁড়া ফাটা নড়বড়ে। বটের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের তীব্র রশ্মি এসে পড়ল ফাজেলের মুখে।ঘুম ভেঙে যেতে লাগলো। অস্বস্থিবোধ করলেন তিনি। মগডালে বসেছিল এক পদ্মগোখরো, সে তা লক্ষ করল। আস্তে আস্তে নেমে এলো নিচে। যে পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যরশ্মি এসে ফাজেলের মুখে পড়েছে ঠিক সেখানে ফণা তুলে দাঁড়ালো সাপটি। ফণার ছায়া এসে পড়ল ফাজেলের মুখে। তিনি আরাম পেয়ে আবারও ঘুমিয়ে পড়লেন।কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে থাকার পর আবার ঘুম ভেঙে গেল। এর মধ্যে ক্লান্তি অনেকটা দূর হয়েছে। কেন যেন বটের পাতায় দৃষ্টি ঘোরাতে লাগলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন সেই সাপটিকে। তখনও ফণা তুলে সূর্যকে আড়াল করে আছে। এবার ফণাটা একটু নড়ে উঠলো, দুলে উঠলো গাছের পাতারা। ফণা নামিয়ে সাপটি হারিয়ে গেল ডালে ডালে পাতায় পাতায়। আবার সূর্যরশ্মি এসে পড়ল ফাজেলের মুখে।তখন তার চোখে ঘুমের রেশ মাত্র নেই। শরীরে নেই একবিন্দু ক্লান্তি। ফাজেল বটতলা ত্যাগ করলেন এবং এলাকার সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ডেকে বললেন, এখানে তোমরা মনসার পূজা দাও।সে দিন ছিল ভাদ্র মাসের শেষ দিন। ১২শ’ বঙ্গাব্দের গোড়ার দিকের কোন এক বছর।তখন থেকেই গুড়পুকুর পাড়ের দক্ষিণে বটগাছতলায় শুরু হয় মনসা পূজা। আর পূজা উপলক্ষে মেলা।সোবহান খান চৌধুরীর পূর্ব পুরুষ ফাজেল খান চৌধুরীর আসল পরিচয় কী তা জানা দরকার।সে আরও অনেক অনেক দিন আগের কথা। তখন বাংলাদেশে সুলতানী শাসন চলছে। বাংলার সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে নতুন নতুন ধারার সূত্রপাত হচ্ছে।ক্রমশ: বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব। মুসলমান সমর নায়ক ও সৈনিকদের পাশাপাশি এদেশে আসতে শুরু করেছে পরিব্রাজক, সাধারণ কর্মচারী, ব্যবসায়ী, ভাগ্যান্বেষী ও সুফি-দরবেশ। সুফি দরবেশরা এসে ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন।সে সময় আরও অনেকের মত এদেশে আসেন উলুঘ খানে আজম খান জাহান (মৃত্যু: ১৪৫৯ খ্রিস্টাব্দ)। খানজাহান আলী নামে পরিচিত।আনুমানিক বাংলা ৯ম শতকের দিকে তিনি বাগেরহাটে ষাটগম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন। যা প্রাক মুঘল স্থাপত্যের এক অতুলনীয় নিদর্শন হিসেবে আজও বিদ্যমান।খানজাহান আলী ষাট গম্বুজ মসজিদে আবস্থান নিয়ে ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। তখন তাঁর দু’জন খাজাঞ্চি ছিলেন। একজনের নাম কামদেব রায় চৌধুরী, জয়দেব রায় চৌধুরী অন্যজন।একদা খানজাহান আলী রোজা থাকা অবস্থায় একটা কমলালেবুর ঘ্রাণ নিচ্ছিলেন, তখন ব্রাহ্মণদ্বয় বললেন, হুজুর আপনিতো আজ রোজা আছেন। এ অবস্থায় কমলার ঘ্রাণ নিলেন, কথায় আছে- ঘ্রাণে অর্ধভোজন।খানজাহান আলী মৃদু হাসলেন- বললেন, তোমাদের সন্দেহ ঠিকই। আমার রোজার আংশিক ক্ষতি হয়েছে।অন্য আর একদিন-খানজাহান আলী নিজেই রান্না করছিলেন। ব্রাহ্মণদ্বয় সেখানে হঠাৎই উপস্থিত হয়ে পড়লেন। বললেন, হুজুর আপনি নিশ্চয় মাংস রান্না করছেন। বড়ই সুঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে। খানজাহান আলী আবারও মৃদু হাসলেন এবং বললেন, তোমরা তো গরুর মাংসের ঘ্রাণ নিয়ে ফেলেছো এখন উপায় কি কামদেব ও জয়দেব চিন্তায় পড়লেন, এবং কয়েকদিন পর খানজাহান আলী এর কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। কামদেব রায় চৌধুরী ও জয়দেব রায় চৌধুরী যথাক্রমে কামালউদ্দীন খান চৌধুরী ও জামালউদ্দীন খান চৌধুরী হয়ে গেলেন। উল্লেখ্য যে, এই কামদেব ও জয়দেব এর কথা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সেই সময়’ উপন্যাসেও বর্ণিত হয়েছে।এ দুজনের মধ্যে কোন একজনের পরবর্তী বংশধর বুড়া খাঁ বাগেরহাট থেকে এসে সাতক্ষীরা শহরের পলাশপোল মৌজায় বাড়িঘর তৈরী করে বসবাস শুরু করেন। গড়ে তোলেন পলাশপোল চৌধুরী বাড়ি। চৌধুরী বাড়ির পূর্বপাশ্বে একটা হোজরখানা দরগা নামে পরিচিত তৈরী করে সেখানে ধর্ম সাধনা করতে থাকেন। হোজরখানাটি বিরাট এক বটগাছ মাথায় করে ভেঙেচুরে এখনও কিছুটা টিকে আছে।বুড়া খাঁ তাঁর বংশধরদের রেখে যান পলাশপোল চৌধুরী বাড়ি। চৌধুরী বাড়ির অধীনে তখন পলাশপোল মৌজার বৃহৎ এলাকা। এলাকাবাসী খাজনা দিতো চেীধুরীদের।বর্তমান সাতক্ষীরা পৌরসভার সবচেয়ে বড় মৌজা পলাশপোল। এটাকে দুটো ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। সেই বাংলা ১২শতকের কোন এক সময় বুড়া খাঁর বংশধর ফাজেল চৌধুরী পলাশপোল এলাকায় খাজনা আদায় করে ফিরছিলেন। সে দিন ছিল ভাদ্র মাসের শেষ দিন। অর্থাৎ ৩১ ভাদ্র। পলাশপোল গুড়পুকুর পাড়ের বটগাছ তলায় বসেন বিশ্রাম নিতে। তখনই ঘটে উপরোক্ত ঘটনাটি। সেই থেকে শুরু হ’ল পূজা ও পূজা উপলক্ষে মেলা। বর্তমানে ওখানে মনসার সাথে বিশ্বকর্মার পূজাও হয়ে থাকে।মেলার নাম গুড়পুকুর আর। বটগাছটার উত্তরে বিশাল দিঘি সদৃশ একটা পুকুর আছে। ঐ পুকুরটার নাম গুড়পুকুর। তারই নামে মেলা। এই নামের জট এখনও খোলেনি। কিভাবে হল এই নামকরণ কেউ বলেন,মনসা পূজার সময় পুকুরে প্রচুর বাতাসা ফেলা হত ওই বাতাসার জন্য পুকুরের পানি মিষ্টি লাগতো, তাই নাম হয়েছে গুড়পুকুর। অনেকের ধারনা পুকুরে পানি থাকতো না বেশি দিন। স্বপ্ন দর্শনে জানা গেল একশ ভাড় গুড় ফেলতে হবে পুকুরে, তবেই পানি থাকবে। স্বপ্ন দর্শন নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করা হল।সেই যে, পুকুরে পানি এলো আর শুকালোনা সারা বছর। আবার শোনা যায় পুকুরের তলদেশ থেকে এক সময় মিষ্টি পানি উঠতো তাই এর নাম হয়েছে গুড়পুকুর। আরো শোনা যায় পুকুরের জায়গাতে অসংখ্য খেজুর গাছ ছিল এবং প্রচুর রস হত ঐ গাছে। একবার গাছের সব রস বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে এই পুকুর কাটা হল। সেই থেকে গুড়পুকুর।আব্দুস সোবহান খান চৌধুরী বললেন, আসলে ওসব কিছু নয় চৌধুরী পাড়ার রায় চৌধুরীরা ছিল গৌর বর্ণের ব্রাহ্মণ, তাই তাদের পুকুরকে বলা হত গৌরদের পুকুর। সেখান থেকে কালক্রমে গুড়পুকুর। গুড়পুকুর সংলগ্ন বটতলায় দোকান ছিল নিতাই কর্মকারের (৭৫)। তিনি আব্দুস সোবহান খানচৌধুরীর মতের সাথে একমত পোষণ করেন।পলাশপোলের বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী ও পৌরসভার কর্মচারী অনিল মজুমদার(৭২)ও একমত হন তবে তিনি বলেন এখানে বিশ্বকর্মার পূজা হয়ে থাকে।সে দিনের গুড়পুকুরের মেলা অনেক বড় হয়েছিল। মেলা শুরু হবার দেড় দু মাস আগ থেকে শুধু সাতক্ষীরা জেলা নয় দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে সাজ সাজ শুরু হয়ে যেত। বিশেষ করে খুলনা, যশোর, সাতক্ষীরার কলম-চারা, কাঠমিস্ত্রি, ফার্ণিচারের কারখানাগুলোতে কাজের তোড়ে ঘুম বিদায় নিতো।ঠকাঠক শব্দে মুখর হয়ে থাকতো এতদ্ব্যঞ্চলের পরিবেশ। ঢাকা, ফরিদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ থেকে আসতেন স্টেশনারি, শিশুতোষ খেলনার দোকানদাররা। পুজা ৩১ ভাদ্র হলেও মেলা চলতো, আশ্বিন মাসের প্রায় শেষ অব্দি।লক্ষ মানুষের সমাগমে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এ এক মহা মিলন স্থলে পরিণত হয়ে যেত। এক সময় তোলা, টোল, চাঁদাবাজদের দৌরাত্মে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা খুব কষ্ট পেয়েছে।সবচেয়ে আকর্ষণ ছিল গাছের চারা-কলম,কাঠের তৈরী বিভিন্ন ফার্ণিচার, কারুশিল্পী নজরুলের পালঙ্ক বিক্রি হ’ত লক্ষাধিক টাকায়।সে পালঙ্ক এক নজর দেখার জন্য মানুষ ভিড় করত। এছাড়াও শিশুদের নানা রকমের খেলনা, মনোহরী দ্রব্যাদি, বাতাবী লেবু, আখ, ইলিশ মাছ। মেলায় এসে আখ-ইলিশ-বাতাবি লেবু ছাড়া কেউ বাড়ি ফিরত না। ছিল বেত শিল্পের নানা দ্রব্য, ধামা, কুলা, দৈড়, লোহার তৈরী দা, বটি, খোন্তা, কোদাল, শাবল প্রভৃতি। অসংখ্য মিষ্টির দোকান।গজা,রসোগোল্লা, ছানা, জিলাপী, কদমা, মুড়ি, বাতাসা, বুটভাজা, বাদাম, চানাচুর কত রকমের খাবার। ছিল মিষ্টি পানের বাহারী আয়োজন। কাঠের আসবাবপত্রের মধ্যে-পিড়ি, দেলকো, বেলন-পিড়ি, খাট-পালঙ্ক, আলনা, আলমারী, চেয়ার টেবিল, ওয়ালড্রব প্রভৃিত। মোটকথা নিত্য ব্যবহার্য সবকিছুই মেলাতে উঠতো। গুড়পুকুর মেলা উপলক্ষে মাসাধিককাল শহরের মানুষের আর অন্য কোন ব্যস্ততা চোখে পড়ত না।মরণ কূপ আসলাম খানের মটর সাইকেল চালনা, সার্কাস খেলা, পুতুল নাচ, যাত্রা, নাগরদোলা। সিনেমা হলে এক টিকিটে দু শো। কি ছিল না গুড়পুকুরকে ঘিরে সারা পলাশপোল, বর্তমানের শহীদ কাজল সরণি, শহীদ নাজমুল সরণি, পাকাপোলের রাস্তা, মোটকথা শহরময় ছড়িয়ে থাকত মেলা। বড় বড় নৌকায় করে আসত সার্কাসের জিনিসপত্র। বাঘ-বানর থাকত খাঁচায় ভরা।হাতি আসত আরো আগে।এসেই শহর ঘুরে বেড়াত আর জানান দিত, সার্কাস এসে গেছে।আমাদের ছোটবেলায় উপভোগ করা মেলারএসব সময়ের আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। আজকের সাতক্ষীরার তরুণ সমাজ যা কল্পনাও করতে পারবে না।মেলা বিস্তৃত হয়েছিল দক্ষিণে আলীপুর পর্যন্ত আর উত্তরে কদমতলা-মাধবকাটি পর্যন্ত। আর এদিক পাটকেলঘাটা।সাধারণত গুড়পুকুরের পাশে, আর পলাশপোলের বিভিন্ন ফাঁকা জায়গা, খালের পাড়, আর রাস্তার দুধারে বসত মেলা।শেষের দিকে এসে ষ্টেডিয়ামে জায়গা নিয়েছিল সার্কাস। ২০০২ সালে স্টেডিয়ামে চলছিল সার্কাস, দর্শকরা উপভোগ করছিল আনন্দে। হঠাৎ বোমা হামলা হয়। শিশুসহ মৃত্যুবরণ করেন তিনজন। বন্ধ হয়ে যায় তিন’শ বছরের প্রাচিন ঐতিহ্যবাহি গুড়পুকুরের মেলা।২০১০ সালে জেলা প্রশাসক, কবি-সংস্কৃতজন মো: আব্দুস সামাদ সাহস নিয়ে এগিয়ে আসেন। মেলা আবার শুরু করেন। শুরু হলেও একে একে মেলা শ্রী হারিয়ে ফেলতে থাকে।স্থানাভাবে স্থান পরিবর্তন হয়। পলাশপোলের মেলা চলে যায় শহীদ আব্দুর রাজ্জাক পার্কে। ক্রমশ লোকজ মেলা হয়ে ওঠে শহুরে মেলা। করেনার কারণে গতবছর মেলা হয়নি। এবছরও সময় চলে গেলো। মেলাটির ব্যবস্থাপনা করে থাকে জেলা প্রশাসন আর পৌরসভা সম্মিলিতভাবে।
এ জাতীয় আরো খবর..










































Leave a Reply